আদর্শিক রাষ্ট্রের পথ: নৈতিকতা, মানবতা ও ইসলামি বিপ্লবের দর্শন
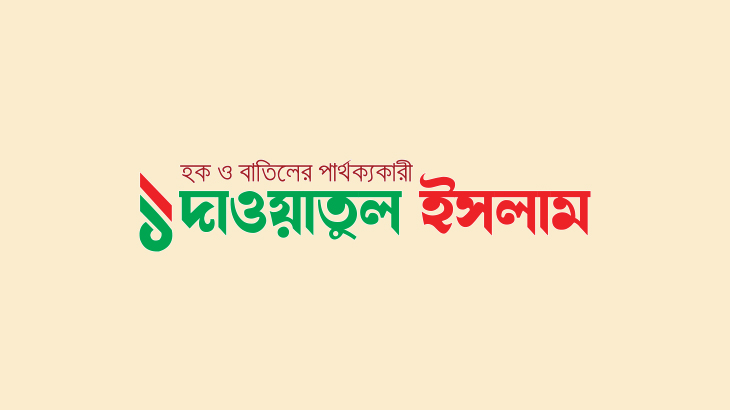
আজকের এই আলোচনায় আমি আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করব—কীভাবে নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে একটি ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।
আজকাল “ইসলামি রাষ্ট্র” শব্দগুচ্ছটি এমনভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যেন এটি শিশুদের খেলনা। এই ধারণাটি কিছু মানুষের কল্পনাকে আকৃষ্ট করেছে, এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ দাবি করেন যে তাঁরা একে জীবনের ইতিবাচক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেসব উপায় প্রস্তাব করা হচ্ছে, সেগুলো এমন অযৌক্তিক যে সেগুলোর সাহায্যে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ঠিক ততটাই অসম্ভব, যতটা অসম্ভব মোটরগাড়িতে চড়ে আমেরিকা পৌঁছানো।
এই ধরনেরঅসংলগ্ন চিন্তাধারার কারণ হলো—কিছু রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণে মানুষের মধ্যে “ইসলামি রাষ্ট্র” নামে একটি আদর্শের আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছে বটে; কিন্তু কেউ বৈজ্ঞানিকভাবে এই রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ধারণের চেষ্টা করেনি, কিংবা কীভাবে এটি বিকশিত হয়—সে প্রক্রিয়াও বিশ্লেষণ করেনি।
এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি এখন দ্বিগুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে—আমাদের উচিত এই সমস্যাটিকেবৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণধর্মীভাবে অনুসন্ধান করা।
রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বাভাবিক বিকাশ
এই শিক্ষিত জনসমাবেশে আমি বেশি সময় ব্যয় না করেই বলতে পারি যে—রাষ্ট্র, যেকোনো প্রকৃতিরই হোক না কেন, কোনো কৃত্রিম উপায়ে গড়ে ওঠে না।রাষ্ট্র এমন কোনো নির্মিত বস্তু নয় যা একটি নির্দিষ্ট স্থানে তৈরি করে মানুষের ইচ্ছামতো অন্য কোথাও স্থানান্তর করা যায়।
বরং রাষ্ট্র হলো এমন একপ্রাকৃতিক সৃষ্টি, যা কোনো অঞ্চলে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান কিছুনৈতিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলাফল।
রাষ্ট্র গঠনের আগে কিছুঅপরিহার্য শর্তপূরণ করতে হয়, কিছুসামাজিক শক্তিতৈরি করতে হয়, এবং কিছুস্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তাপূর্ণ করতে হয়—তারপরই ঘটনাপ্রবাহের চাপে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।
যেমন যুক্তিবিদ্যায় (Logic) উপসংহার সবসময় পূর্বনির্ধারিত উপপাদ্যের বিন্যাস অনুসারে আসে, কিংবা রসায়নে (Chemistry) নির্দিষ্ট রাসায়নিক উপাদান নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশলে নির্দিষ্ট যৌগই তৈরি হয়—তেমনি সমাজবিজ্ঞানে (Sociology) রাষ্ট্রও হলো সেই সমাজে পূর্ব থেকে বিদ্যমান পরিস্থিতির স্বাভাবিক পরিণতি।
আবার, রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয় সেই পরিস্থিতির প্রকৃতির দ্বারা, যার ভেতর থেকে রাষ্ট্রের জন্ম হয়।
যেমন:
ঠিক তেমনি, যদি কোনো সমাজে এমন পরিস্থিতি বিরাজ করে যা এক বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য উপযোগী, এবং সেই পরিস্থিতির পারস্পরিক ক্রিয়াও সেই একই ধরনের রাষ্ট্রের বিকাশের অনুকূল হয়, তবে সেই দীর্ঘ বিবর্তন প্রক্রিয়ার শেষে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রের উদ্ভব হবে—এমনটা কখনোই সম্ভব নয়।
অতএব, যে শক্তি ও উপাদান কোনো নির্দিষ্ট ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে সহায়ক, সেই একই শক্তির প্রভাবে ভিন্ন প্রকৃতির রাষ্ট্রের জন্ম হওয়া একেবারেই অসম্ভব।
এখানে আমি যেননিয়তিবাদের (Determinism)তত্ত্ব প্রচার করছি এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে
অস্বীকার করছি—এমনটি যেন কেউ মনে না করেন।
নিঃসন্দেহে, একটি রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ধারণেব্যক্তি ও সমাজের ইচ্ছা এবং কার্যকলাপগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
আমি যা বলতে চাই তা হলো—যে ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করতে চাওয়া হচ্ছে, সেই রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি ও আত্মার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায় ও পথইবেছে নিতে হবে। শুধুমাত্র লক্ষ্য নির্ধারণ করলেই চলবে না; সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপযুক্তনীতি, সংগঠন, নেতৃত্ব ও নৈতিক সংস্কৃতিগড়ে তুলতে হবে।
অর্থাৎ—
· সেই রাষ্ট্রব্যবস্থার চেতনায় উদ্বুদ্ধ এক ধরনের আন্দোলন গড়ে উঠতে হবে;
· জনগণের চরিত্র ও মানসিকতা সেই চেতনায় রূপান্তরিত হতে হবে;
· একই মানসিকতার কর্মীবাহিনী তৈরি করতে হবে;
· এবং এমন নেতৃত্বের উত্থান ঘটাতে হবে যা রাষ্ট্রব্যবস্থার সেই আদর্শিক রূপের সঙ্গে মানানসই।
যখন এই উপযুক্ত উপায়গুলো সফলভাবে প্রয়োগ করা হবে, এবং প্রয়োজনীয় সব শক্তি ও উপাদান দীর্ঘ সময়
ধরে কাজ করতে থাকবে, তখনই তাদের
প্রভাবে এমন একসামাজিক কাঠামোতৈরি হবে যা নিজস্ব চেতনার বাইরে অন্য কোনো প্রভাব সহ্য
করতে পারবে না।
ফলত, এই প্রক্রিয়ারস্বাভাবিক পরিণতিহিসেবে সেই নির্দিষ্ট
ধরনের রাষ্ট্রেরই জন্ম হবে—যার ভিত্তি এই সব শক্তি ও প্রক্রিয়া পূর্বেই তৈরি করে
রেখেছিল।
এটা অনেকটা যেমন একটিবীজ থেকে গাছ জন্ম নেয়, নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি দিয়ে ক্রমে বৃদ্ধি পায়, এবং পরিণত বয়সে সেইধরনেরই ফলদেয় যার জন্য তার প্রকৃতি উপযুক্ত ছিল।
এই সত্যটি অনুধাবন করলে বোঝা যাবে—যদি কোনো সমাজে একটি নির্দিষ্ট প্রকারের আন্দোলন, নেতৃত্ব, গণচরিত্র ও নৈতিকতা গড়ে ওঠে, যা একটি বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অথচ প্রত্যাশা করা হয় যে এর ফলস্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র সৃষ্টি হবে—তাহলে সেটি হবে নিছকঅবাস্তব কল্পনা, বা বলা চলেবাস্তবতাবিবর্জিত আশা।
আদর্শিক রাষ্ট্র (The Ideological State)
এখন আমাদের
বিবেচনা করতে হবে, যে রাষ্ট্রকে আমরা “ইসলামি রাষ্ট্র” বলি,
তার প্রকৃতি
আসলে কী।
এই বিষয়ে আমি
প্রথমেই বলতে চাই যে, ইসলামি রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যহলো—এটিজাতীয়তাবাদের
সব চিহ্ন ও প্রভাব, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ—সবকিছুর থেকেই সম্পূর্ণ মুক্ত।
ইসলামি রাষ্ট্র
গঠিত হয়শুধুমাত্র নীতির ভিত্তিতে,
কোনো বংশ,
জাতি বা
ভূখণ্ডের ভিত্তিতে নয়।
এই অর্থে আমি
একে বলব একটিআদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র (Ideological
State)।
এমন একটি
রাষ্ট্র, যার ভিত্তি স্থাপিত হয়স্বীকৃত নৈতিক
নীতিমালার ওপর, এবং যাজাতি বা বর্ণবোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত—
এমন রাষ্ট্রের
দৃষ্টান্ত মানবসভ্যতার ইতিহাসেমাত্র একবারইদেখা গেছে।
কিন্তু দুঃখজনক
হলো, আজও
মানবজাতি সেই রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃত গুরুত্ব ও সুবিধা উপলব্ধি করতে পারেনি।
প্রাচীন যুগে
মানুষ শুধুপরিবার বা বংশভিত্তিক শাসনব্যবস্থাচিনত।
তারপর এলজাতিগত
ও জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা।
কিন্তু এমন একটি
রাষ্ট্রের ধারণা—
যাএকটি
নির্দিষ্ট নৈতিক ও আদর্শিক নীতিমালার ওপরপ্রতিষ্ঠিত,
এবং যার
শাসকগোষ্ঠী গঠিত হয়বিভিন্ন জাতি ও অঞ্চলের মানুষদের দ্বারা,
যারা নিজেদের
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি হিসেবে ঐ আদর্শকে
স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে—
এমন চিন্তা
মানবজাতির সংকীর্ণ মস্তিষ্কে কখনো দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়নি।
খ্রিস্টধর্মএই
সত্যটিকে কিছুটা আভাসে ধারণ করেছিল,
কিন্তু সে এর
ওপর ভিত্তি করে পূর্ণাঙ্গ আদর্শ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করতে পারেনি।
ফরাসি বিপ্লবেওআমরা
এক ঝলকের মতো দেখি—একটি আদর্শনির্ভর রাষ্ট্রব্যবস্থার চেষ্টা,
কিন্তু তা শিগগিরইজাতীয়তাবাদের
অন্ধকারে হারিয়ে যায়।
কমিউনিজমঅবশ্য
এই আদর্শিক রাষ্ট্রের ধারণা গভীরভাবে প্রচার করেছিল
এবং এমন রাষ্ট্র
প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করেছিল।
রাশিয়ার
বিপ্লব-পরবর্তী সময়কালে বিশ্ব একসময় সেই “মহান রুশ পরীক্ষা” নিয়ে আগ্রহী হয়েছিল।
কিন্তু অচিরেইজাতীয়তাবাদের
বিষসেই কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকেও গ্রাস করেছিল—
মূল পর্যন্ত তার
আদর্শকে কলুষিত করে দেয়।
মানব ইতিহাসের
প্রারম্ভকাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত,
শুধুমাত্র
ইসলামইএমন একটি ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছে
যা একটি
রাষ্ট্রকেসম্পূর্ণ আদর্শের ভিত্তিতেসংগঠিত করতে চায়,
যাজাতীয়তাবাদ
ও বর্ণবৈষম্যের সকল প্রভাব থেকে মুক্ত,
এবং যাসমস্ত
মানবজাতিকে আহ্বান করে
এর আদর্শ
গ্রহণের মাধ্যমেএকটি অজাতিক, আদর্শিক রাষ্ট্রগঠনে
অংশ নিতে।
যেহেতু এটি একটি নতুন বিষয় এবং আমাদের চারপাশের পৃথিবী কেবল অমুসলিমরাই নয়, এমনকি মুসলমানরাও এর সম্পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে অক্ষম, তাই এই ধারণাটি সেইসব মুসলমানদের ধারণার বাইরে চলে যায় যারা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও পশ্চিমা ধারায় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা লাভ করেছেন এবং জীবন ও ইতিহাস সম্পর্কে যাদের দৃষ্টিভঙ্গি ইউরোপীয় ইতিহাস এবং পশ্চিমা রাজনীতি থেকে ধার করা হয়েছে। এর ফলে ভারতের বাইরের যেসব দেশে মুসলিমরা প্রাধান্য পেয়েছে এবং যারা কমবেশি স্বাধীন, সেখানে যখন এই ধরণের লোকেরা সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন তারা জাতীয় সরকার এবং জাতীয় রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোনও সরকার বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা ভাবতে পারে না। এর কারণ ছিল ইসলাম এবং জীবনের সমস্যাগুলির প্রতি তার মনোভাব সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না এবং জাতি বা জাতীয়তার নীতির পরিবর্তে নির্দিষ্ট নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নীতির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের কোন ধারণা ছিল না। ভারতেও, যারা একই ধরণের ‘মানসিক প্রশিক্ষণ’ পেয়েছে তারা একই ভ্রান্ত ধারণার সাথে জড়িত। তারা একটি ‘ইসলামী রাষ্ট্র’ সম্পর্কে কথা বলে কিন্তু তাদের অদ্ভুত মানসিক প্রশিক্ষণ এবং পশ্চিমা রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমির কারণে, তাদের মনে ‘ইউরোপের একটি ‘জাতীয় রাষ্ট্র’-এর জীবন ও ইতিহাস থেকে উদ্ভূত ‘জীবনের কোনও পরিকল্পনা’ নেই। সচেতনভাবে বা অজ্ঞাতসারে, তারা জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের ‘শিকার’ হয়ে পড়ে; এবং তারা যে কর্মসূচির কথাই ভাবেন না কেন, তা ‘মৌলিকভাবে জাতীয়তাবাদী’। তাদের মতে, আমাদের মুখোমুখি ‘সমস্যা’র প্রকৃতি এই যে: মুসলমানরা হিন্দু, ইংরেজ এবং ফরাসিদের মতো একটি ‘পৃথক জাতীয় গোষ্ঠী এবং ‘তাই তাদের নিজস্ব ‘রাষ্ট্র ও সরকারের অধীনে একটি পৃথক জাতীয় অস্তিত্বের অধিকার রয়েছে’। তারা যতই তাদের ‘মস্তিষ্ককে তাড়া করুক না কেন, তারা এই ‘উদ্দেশ্য অর্জনের’ অন্য কোনও উপায় কল্পনাও করতে পারে না, কেবল এই যে, একটি জাতি হিসেবে, মুসলমানদের একই ‘পদ্ধতি’ অনুসরণ করা উচিত এবং ইতিহাসের অন্যান্য সমস্ত জাতীয় গোষ্ঠী যে কৌশল অনুসরণ করেছে এবং ‘গ্রহণ করেছে’ তা গ্রহণ করা উচিত। অন্য কথায়, ‘এই জাতীয়তা যে উপাদানগুলির সমন্বয়ে গঠিত, সেগুলিকে প্রথমে একত্রে একত্রিত করা উচিত
একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ সমগ্রে একত্রিত করা উচিত; একটি শক্তিশালী জাতীয় চেতনা
তারপর তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করা উচিত; একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের আবির্ভাব হওয়া উচিত এবং
তাদের নির্দেশ দেওয়া উচিত; তাদের নিজস্ব জাতীয় রক্ষীদের সংগঠিত করা উচিত; তাদের
একটি জাতীয় মিলিশিয়া থাকা উচিত; যেখানেই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হোক না কেন, তাদের
সুপরিচিত গণতান্ত্রিক ‘সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের নীতি’র উপর ভিত্তি করে একটি জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করা উচিত; এবং যেখানেই তারা সংখ্যালঘু হোক না কেন,
তাদের "অধিকার" সুরক্ষিত করা উচিত এবং তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সুরক্ষিত করা উচিত,
ঠিক যেমন জাতীয় সংখ্যালঘু শব্দের অন্যান্য দেশে তারা এই সুরক্ষা চায় এবং
দাবি করে: পরিষেবা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং
নির্বাচিত সংস্থাগুলিতে, তাদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত, তাদের
প্রতিনিধিদের তাদের নিজস্ব ভোটে নির্বাচিত করা উচিত; এবং
একটি স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা হিসেবে মন্ত্রিত্বে তাদের যথাযথ অংশ দেওয়া উচিত।
এইসব মানুষের পদ্ধতি এবং ধারণা এই রকম। তারা স্পষ্টতই
ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণা থেকে ধার করা এবং তবুও
যারা উপরোক্ত উপায় এবং কৌশলের পক্ষে কথা বলেন তারা একই সাথে একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের তাদের সংকল্পের কথা বলেন। এই লোকেরা ইসলামী
পরিভাষা, 'উম্মাহ' 'মিল্লাত', 'আমির' এবং 'আমিরের আনুগত্যের কর্তব্য' ব্যবহার করে, যার অর্থ ইসলামী পরিভাষায় এই ব্যক্তিরা যখন এই
শব্দগুলি ব্যবহার করেন তখন তাদের মনে যা থাকে তার থেকে বেশ ভিন্ন। তবে তাদের কাছে এই ইসলামিক পরিভাষাগুলি জাতীয়তাবাদের পরিভাষার সমার্থক এবং ভাগ্য ভালো যে, এই পরিভাষাগুলি ইসলামী সাহিত্যে তৈরি অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল এবং এখন পশ্চিমা বিশ্ব থেকে উদ্ভূত অনৈসলামিক ধারণা এবং কর্মপদ্ধতির আবরণ হিসেবে অবাধে ব্যবহৃত হচ্ছে।
আদর্শিক রাষ্ট্রের নৈতিক ও আত্মিক ভিত্তি
যদি আপনি এমন
একটি রাষ্ট্রের প্রকৃতি বোঝেন—যার ভিত্তিআধ্যাত্মিক ও নৈতিক নীতির ওপরপ্রতিষ্ঠিত—
তাহলে সহজেই
উপলব্ধি করতে পারবেন যে, যেসব চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা বর্তমানে প্রচলিত,
তা এমন রাষ্ট্র
গঠনেরশুরু করার জন্যও উপযুক্ত নয়,
শেষপর্যায়ে তার
সফলতা তো দূরের কথা।
বরং,
এই ধরনের চিন্তা
ও কাজের ধারা প্রকৃতপক্ষেএকটি অজাতিক বা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের
বিকাশের জন্য ক্ষতিকর ও বিধ্বংসী।
একটি আদর্শিক
রাষ্ট্রের মূলভিত্তি হলো—
আমরাগোত্র,
শ্রেণি,
জাতি বা
জাতীয়তার সমস্ত প্রশ্নকে প্রত্যাখ্যান করি,
এবং মানুষকে
দেখিনৈতিক ও আত্মিক সত্তা হিসেবে,
জাতিগত বা
ভৌগোলিক সত্তা হিসেবে নয়।
আমাদের উদ্দেশ্য
মানুষেরজাতীয় পরিচয় নয়, বরং মানবিক পরিচয়।
আমরা তাদের
সামনে উপস্থাপন করিকিছু আদর্শ ও নীতিমালা,
এবং সেই
নীতিগুলির উৎস হিসেবে তুলে ধরিবিশ্বাসের একটি ভিত্তি,
যার ওপর দাঁড়িয়ে
আমরা দাবি করি—
এই নীতিগুলোই
হতে পারেএকটি সার্বজনীন সভ্যতা ও অজাতিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি,
যা মানবজাতিকেএই
পৃথিবীতেও শান্তি দেবে এবং পরকালেও মুক্তি দান করবে।
যে কেউ এই
নীতিগুলোকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবে,
সে-ই হবেএই
রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিচালনায় সমান অংশীদার—
তার জাতি,
ভাষা বা বর্ণ
যাই হোক না কেন।
এখন প্রশ্ন হলো—
একজন ব্যক্তি
যার চিন্তা, কর্ম ও কর্মকাণ্ডেজাতীয়তাবাদের ছাপ স্পষ্ট,
সে কীভাবে এমন
একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে পারে?
সে কীভাবে সমগ্র
মানবজাতির কাছে মানবতার আহ্বান জানাবে,
যখন সে নিজেই
একটি বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের স্বার্থে আবদ্ধ?
সে যদি নিজ
জাতির মঙ্গলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখে,
তাহলে একইসঙ্গেমানবতার
নামে ও সার্বজনীন কল্যাণের নামেআহ্বান জানানো কি যুক্তিসঙ্গত?
এটা কি হাস্যকর
নয়—
যারা নিজেদের
জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতায় অন্ধ,
যারা জাতির নামে,
জাতির অধিকারের
নামে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে,
তাদের উদ্দেশে
কেউ যদি মানবতার কথা বলে,
আর সেই সঙ্গে
নিজের জাতির জন্য “জাতীয় অধিকার” ও “স্বাধীনতা” দাবি করে—
তাহলে সেটি কিনৈতিকভাবে
আত্মবিরোধী নয়?
যেমন,
যদি কেউ মানুষকে
মামলা-মোকদ্দমা থেকে বিরত রাখতে চায়,
কিন্তু নিজের
অবস্থান থেকেআদালতে মামলা দায়ের করেই সেই প্রচার শুরু করে,
তবে সেটি যেমনবিরোধাভাসপূর্ণ
ও হাস্যকর,
তেমনিজাতীয়তাবাদী
মানসিকতা নিয়ে আদর্শিক রাষ্ট্রের আহ্বান জানানোও আত্মঘাতী।